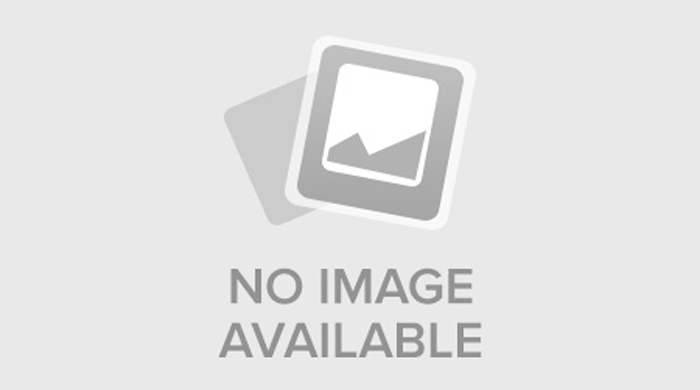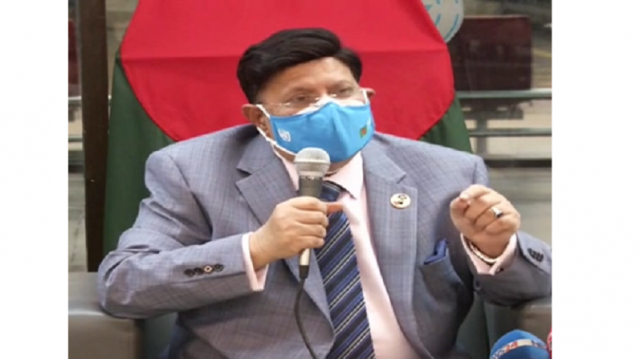স্বপ্নে কেন দৌড়ানো যায় না?

আপনি নিশ্চয়ই এমন স্বপ্ন অনেকবার দেখেছেন—খুব ভয়ঙ্কর কিছু থেকে বাঁচতে দৌড়াতে চাইছেন। হয়তো কেউ আপনাকে তাড়া করছে, ভয়ানক সাপ ছুটে আসছে, অথবা আপনি এমন কোনো বিপদে পড়েছেন যেখান থেকে পালানো ছাড়া উপায় নেই। অথচ বারবার চেষ্টা করেও আপনি ঠিকভাবে দৌড়াতে পারছেন না। পা যেন আটকে আছে, মনে হয় শরীরটাই কাজ করছে না। তখন স্বপ্নটা ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্নে রূপ নেয়।
প্রশ্ন হচ্ছে, স্বপ্নে আমরা কেন দৌড়াতে পারি না? স্বপ্নে অন্য সব কাজ যখন সহজে সম্ভব হয়—উড়া, লাফানো, এমনকি কিছু অলৌকিক ঘটনাও—তখন দৌড়ানোর মতো সাধারণ কাজটাই কেন সম্ভব হয় না?
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের একটু ঘুম এবং মস্তিষ্কের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে হবে।
মানুষের ঘুম মূলত দুই ধাপে বিভক্ত—নন-রেম (Non-REM) ও রেম (REM)। রেম-এর পুরো মানে হলো Rapid Eye Movement, অর্থাৎ ‘দ্রুত চোখ নড়াচড়া করা’। এই ধাপেই মানুষ সবচেয়ে বেশি স্বপ্ন দেখে। রেম ধাপে আমাদের মস্তিষ্ক অনেকটাই জেগে থাকার মতো সক্রিয় হয়ে পড়ে, কিন্তু শরীর তখন একেবারে স্থির থাকে।
এই সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন যেমন নরএপিনেফ্রিন, সেরাটোনিন ও হিস্টামিন নিঃসরণ বন্ধ থাকে, যার কারণে আমাদের পেশিগুলো কার্যত অবশ বা অচল হয়ে যায়। একে বলা হয় “REM atonia” বা রেম ধাপে পেশির অসাড়তা। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এটা আমাদের শরীরকে স্বপ্ন অনুযায়ী বাস্তবে চলাফেরা করা থেকে বিরত রাখার জন্যই ঘটে। যেমন আপনি যদি স্বপ্নে কাউকে ঘুষি মারেন, বাস্তবে যেন ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার হাত না উঠে আসে।
এমনকি গবেষণায় দেখা গেছে, যাদের এই পেশিগুলো পুরোপুরি বন্ধ হয় না, তাদের ঘুমের মধ্যে হাঁটার সমস্যা (Sleepwalking) হতে পারে। অর্থাৎ রেম ধাপে পেশি নিস্তেজ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ও নিরাপদ ঘুমেরই একটা অংশ।
যখন আপনি স্বপ্নে দৌড়ানোর চেষ্টা করেন, তখন আসলে আপনার মস্তিষ্ক দৌড়ানোর চিন্তা করে ঠিকই, কিন্তু শরীরের পেশি তো তখন নিষ্ক্রিয়। তাই আপনি হয়তো নিজেকে খুব ধীরগতিতে চলতে দেখেন, বা পা যেন আটকে আছে এমন মনে হয়। এই অভিজ্ঞতাটাই স্বপ্নে “দৌড়াতে না পারা”র অনুভূতি তৈরি করে।
এটা শুধু দৌড়ানো নয়, আরও অনেক কাজের ক্ষেত্রেই হয়। অনেকেই স্বপ্নে দেখেন, তারা পরীক্ষার হলে পৌঁছাতে পারছেন না, বা খাতায় লিখতে গেলে হাত কাজ করছে না। আবার কেউ কেউ চিৎকার করতে চাইলেও করতে পারেন না। কেন এমন হয়?
এর পেছনেও আছে মস্তিষ্কের কাজের ব্যাখ্যা। ভাষা ও হাতের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ—Broca’s area ও Wernicke’s area। স্বপ্ন দেখার সময় এই অংশগুলো সম্পূর্ণভাবে সক্রিয় থাকে না। তাই ভাষা ঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় না, এবং সেই সাথে হাতের সূক্ষ্ম কাজও (যেমন লেখা) ব্যাহত হয়।
স্বপ্নকে অনেক সময় বলা হয় আমাদের অবচেতন মনের আয়না। প্রতিদিনের চিন্তা, দুশ্চিন্তা, ভয়, ইচ্ছা এসবই স্বপ্নে নানা রূপে ফিরে আসে। পরীক্ষা নিয়ে যদি কেউ দুশ্চিন্তায় থাকে, তাহলে স্বপ্নে পরীক্ষা দিতে না পারা বা খাতা হারিয়ে ফেলার দৃশ্য দেখা খুব সাধারণ।
আবার কেউ যদি জীবনে কোনো দুঃসময় পার করছে বা ভয়ের মধ্যে আছে, তাহলে তার স্বপ্নেও সেই ভয় নানা রূপে হাজির হতে পারে। দুঃস্বপ্নগুলো যেন মনেরই একধরনের সিগন্যাল, যা বলে—”তোমার মানসিক চাপ আছে, একটু বিশ্রাম দরকার।”
স্বপ্নে দৌড়াতে না পারা, কিছু করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হওয়া, এসব একধরনের মানসিক অস্বস্তির প্রতিফলন। মাঝে মাঝে এগুলো স্বাভাবিক, কিন্তু যদি এমন স্বপ্ন বারবার আসে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়, বা আপনি দিনভর চাপে থাকেন, তাহলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত।
বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের অনেক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে, পর্যাপ্ত রেম ঘুম না হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়, চিন্তাশক্তি কমে যায়, এমনকি মানসিক অস্থিরতা বাড়ে। তাই ভালো ঘুম ও মানসিক স্বাস্থ্য একে অন্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।
স্বপ্নে দৌড়াতে না পারা বা কোনো কাজে সফল না হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। এর পেছনে লুকিয়ে থাকে ঘুমের ধাপ, মস্তিষ্কের কার্যক্রম এবং আমাদের অবচেতন মানসিক অবস্থা। এগুলোর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থাকলেও, অনেক সময় এগুলো আমাদের জীবনের চিন্তা ও চাপে ঘিরে গড়ে ওঠে।
তাই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভালো ঘুম, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও মানসিক প্রশান্তি—এই তিনটি জিনিস নিশ্চিত করলে দুঃস্বপ্ন কমে যাবে, আর আপনি হয়তো একদিন স্বপ্নেই উড়েও বেড়াতে পারবেন—পায়ের টানাটানি ছাড়াই!
সূত্র: ল্যানসেট